সর্বশেষ
মঙ্গলবার, ২ আগস্ট, ২০১৬
রবিবার, ৩১ জুলাই, ২০১৬
মেছো বিড়াল
নৃ-গোষ্ঠীঃ রাজবংশী
রাজবংশীরা মূলত কৃষিজীবী, তবে মাছধরা এবং মাছ বিক্রয় এদের অন্যতম পেশা। মেয়েরা কুটির শিল্পের কাজে দক্ষ। পিতাই পরিবারের প্রধান। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তাদেরকে ধর্মীয় আচারে শৈব বলে মনে করা হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক প্রভৃতি বিশ্বাসের সমন্বয়ে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তারা মহাকাল শিব, বিষহরী (মনসা)র আরাধনা করেন এবং একই সঙ্গে দুর্গা, কালী (শ্যামা), লক্ষ্মী, জগন্নাথ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীরও পূজা করে। দেবদেবীর পূজার পাশাপাশি প্রাচীন কৃষিসংস্কৃতির প্রতীক ‘বারিধারা’ ব্রত কিংবা উর্বরতা ও প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রত বা অনুষ্ঠানাদি পালন করে। এরা প্রকৃতি উপাসকও বটে এবং পাহাড়, নদী, অরণ্য ও মৃত্তিকার পূজা করে থাকে। এরা ঘর-সংসারের মঙ্গল কামনায় বাস্ত্তদেবতা বাহাস্তো বা বাহুস্তো এবং শস্য রোপণের পূর্বে বলিভদ্র ঠাকুরের পূজা করে। এদের পূজা-পার্বণে নৃত্যগীতোৎসব আদিবাসীসুলভ সামাজিক প্রথারূপেই ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খরা, অনাবৃষ্টি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ‘হুদুমা’ পূজা রাজবংশীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।
রাজবংশী নারীদের ব্যবহৃত গহনা
রাজবংশীদের কোন লেখ্য ভাষা বা বর্ণমালা নেই। এদের ভাষা স্থানিক তথা আঞ্চলিক ভাষার এক
মিশ্ররূপ। এরা যে আঞ্চলিক মিশ্র ভাষায় কথা বলে তা কারও কারও বিচারে ‘বিকৃত’ বাংলা।
রাজবংশীদের বিবাহ প্রথায় সাঁওতাল, ওরাওঁদের বিবাহরীতির প্রভাব যথেষ্ট। বিবাহ বিচ্ছেদ,
পুনর্বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত। তবে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে দেবরদের দাবি
অগ্রগণ্য। রাজবংশীরা মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার কাজ সম্পন্ন করে। একমাস পর মৃত ব্যক্তির
জন্য শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।
রাজবংশীদের ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্র
তথ্যসুত্রঃ আহমদ রফিক (বাংলাপিডিয়া),
ছবিঃ সংগ্রহ
সবুজ ময়ূর
সবুজ ময়ূর (Pavo muticus) (ইংরাজি: Green Peafowl) বা বর্মী ময়ূর Phasianidae (ফ্যাসিয়ানিডি) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Pavo (পাভো) গণের অসাধারণ সুন্দর, ঝলমলে রাজকীয় ময়ূর। সবুজ ময়ূরের বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ ছোট ময়ূর (ল্যাটিন: pavo = ময়ূর; muticus = ছোট, ক্ষুদে বা সংক্ষিপ্ত)। সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় ৯ লাখ ৯১ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আবাসস্থল এত বিশাল হলেও পুরো এলাকাটির মাত্র অল্পসংখ্যক এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে এদের বিস্তৃতি রয়েছে। আবার বিগত কয়েক দশকে এদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেকারণে আই ইউ সি এন এই প্রজাতিটিকে Endengered
বা বিপন্ন বলে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে একসময় এরা প্রচুর পরিমাণে থাকলেও সম্প্রতি এদের দেখতে পাওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।
- P. m. spicifer (Shaw & Nodder, 1804) – উত্তর-পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম মিয়ানমারে এদের সহজেই দেখা মিলত। এই উপপ্রজাতিটি সম্ভবত বিলুপ্ত (Possibly extinct)। উপপ্রজাতিটিতে নীলের ভাগ বেশি ও উজ্জ্বলতা বেশ কম।
- P. m.imperator (Delacour, 1949) – মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও চীনে এদের দেখা যায়। P. m.imperator প্রায় muticusএর মতই, তবে দেহতল বেশি গাঢ় ও চোখের পাশের হলুদ ছোপটি কম উজ্জ্বল।
- P. m. muticus (Linnaeus, 1758) – কেবলমাত্র ইন্দোনেশিয়ার জাভায় দেখা যায়। একসময় মালয় উপদ্বীপে বিস্তৃত থাকলেও সে এলাকায় এরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। উপপ্রজাতিগুলোর মধ্যে এই উপপ্রজাতিটি সবচেয়ে উজ্জ্বল সবুজ আর এর ডানার পালকে গাঢ় সবুজ ও নীল বর্ণ থাকে।
শনিবার, ৩০ জুলাই, ২০১৬
শকুনঃ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে
মৃতপ্রাণী খায় বলে একে মাংসাশি পাখি বলে। এর দেহ বিশাল। ডানা প্রশস্ত। দেহের রঙ কালচে। মাথা ও ঘাড় পালকহীন। কান লতিকাহীন। ঠোঁট সরু ও লম্বা। লেজের পালক সংখ্যা ১২-১৪টি। এর দৈর্ঘ্য ৯০ সেমি, ওজন ৪.৩ কেজি, ডানা ৫৫ সেমি, ঠোঁট ৭.৬ সেমি, পা ১১.৬ সেমি ও লেজ ২২.৫ সেমি। এদের খাবারের তালিকায় রয়েছে মৃতপ্রাণী ও পচামাংস। সেপ্টেম্বর-মার্চ মাসে এরা ডিম পাড়ে মাত্র একটি করে। ডিমের মাপ ৮.৬ গুণ ৬.৪ সেমি। ৪৫ দিনের মাথায় এদের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। উঁচু গাছ বা দালানে ডালপালা দিয়ে মাচার মতো করে বাসা বানায় এরা। আর এক বাসাতেই থাকে বছরের পর বছর।
টুনটুনি
টুনটুনি বিভিন্ন রকম খাবার খায়। এরা অনেক অপকারী পোকামাকড়,কীটপতঙ্গ খাদ্য হিসেবে খায়। তাছাড়াও ছোট কেঁচ, মৌমাছি, ফুলের মধু, রেশম মথ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে। ধান-পাট-গম পাতার পোকা, শুয়োপোকা ও তার ডিম, আম পাতার বিছা পোকা তাদের খাদ্য তালিকায় আছে। টুনটুনির বাসা খুব বেশি উচুতে হয়না। সাধারনত এরা ৬-১০ সেমি উচ্চতায় বাসা বাধে। ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ অথবা ঝোপঝাড় এদের প্রধান পছন্দ।শিম, লাউ, কাঠ বাদাম, সূর্যমূখী, ডুমুর, লেবু এগুলো গাছে এরা বেশি বাসা বাধে।পুরুষ ও স্ত্রী পাখি মিলে বাসা তৈরী করে।
বাংলাদেশের ফুলসমূহ
বুধবার, ২৭ জুলাই, ২০১৬
'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ'
'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ'
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
প্রাচীন ঐতিহ্য পালকি
প্রাচীন ঐতিহ্য ঢেঁকি
কালের আর্বতনে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো। তেমনি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি শিল্প আজ হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের ঘরে এখন আর এগুলো আগের মত চোখে পড়ে না। ভোরে আজানের সাথে সাথে স্থদ্ধতা ভেঙ্গে ঢেঁকির শব্দ এখন আর ছড়িয়ে পড়েনা চারিদিগে। চোখে পড়ে না বিয়ে সাদির উৎসবে ঢেঁকি ছাটা চালের ক্ষির পায়েস রান্না। অথচ একদিন গ্রাম ছাড়া ঢেঁকি কিংবা ঢেঁকি ছাড়া গ্রাম কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেখানে বসতি সেখানেই ঢেঁকি কিন্তু আজ তা আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য থেকে মুছে যাচ্ছে। এই গ্রাম বাংলার ঢেঁকি নিয়ে কবি – সাহিত্যিক রচনা করেছেন কবিতা গল্প। বাউলরা গেয়েছেন গান। আগে গ্রামের প্রায় বাড়িতেই ঢেঁকিতে ধান ভানতো। জীবিকা অর্জনের মাধ্যম ও ছিল।
এটা পূর্বের তুলনায় তা আজ দেখা যায় না। অনেকই এ পেশায় জড়িত ছিল। বর্তমানে তারা পেশাচ্যুত। তাদের অনেকেই এখন কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বলা হয় তারানী। আগে ঢেঁকি শিল্পে জড়িত ছিল অনেকে। এরা সবাই বাধ্য হয়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। কেউ কাঁথা সেলাই কেউবা দর্জির কাজ করেন , আবার কেউ কেউ ভিক্ষা বৃওি ও ঝি-এর কাজ করছে। করছে হাঁস- মুরগী পালন। গ্রামের লোকেরা এখন আর আগের মতো ঢেঁকিতে ধান ছাটাই করে না। প্রায় গ্রামে মিনি রাইস মিল গড়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এখন লেখাপড়া শিখছে। তাই বড়দের এখন কেউ ঢেঁকিতে পাড় দিতে দেয় না। তা ছাড়া মেয়েরা যদি একটু লেখাপড়া জানে তবে শ্বশুর বাড়ি এসে ঢেঁকিতে পাড় দিতে ধান ভানতে চায় না। সেজন্য গ্রামে এখন ঢেঁকি দেখা যায় না। গ্রাম-গঞ্জেএখন শত শত মিনি রাইস মিল গড়ে উঠেছে। মানুষ শিক্ষিত হয়েছে। রুচি ও গেছে বদলে। ফলে ঢেঁকি অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে প্রায়। হাজার হাজার বিধবা তালাক প্রাপ্ত এবং গরীব মহিলাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল ছিল এই ঢেঁকি। গ্রামে গেলে কারো কারো বাড়িতে ঢেঁকি দেখা যায়। কিন্তু এতে এখন আর ধান ভানা হয় না। গোয়াল ঘরে কিংবা অন্য কোথাও পরিত্যক্ত রয়েছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন ঢেঁকি দেখার জন্য হয়তো বা যাদুঘরে যেতে হবে।
ছবি: গ্রামের নারীদের চাল ভাঙ্গানোর দৃশ্য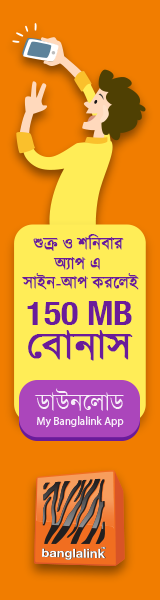


















.jpg)











